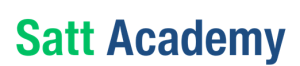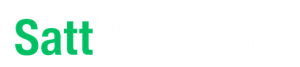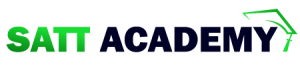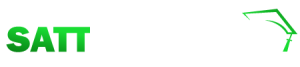স্থিতি ও গতি আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার বিষয়। এ বিশ্বে কোনো বস্তু স্থির আবার কোনো বস্তু গতিশীল। প্রতিদিন আমাদের আশেপাশে নানা রকম স্থিতি ও গতি দেখতে পাই। বাড়িঘর, দালান- কোঠা, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট, রাস্তার পাশে গাছ সব সময়ই দাঁড়িয়ে আছে-এরা স্থিতিতে আছে বা স্থির। চলমান বাস, চলন্ত গাড়ি, চলন্ত রিক্সা, চলন্ত ট্রেন এমনকি আমাদেরও হাঁটা-চলা হলো গতির উদাহরণ। এ অধ্যায়ে আমরা স্থিতি ও গতি নিয়ে আলোচনা করব।
এই অধ্যায় শেষে আমরা
- স্থিতি ও গতির পার্থক্য করতে পারব।
- সকল গতিই আপেক্ষিক তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার গতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশিসমূহের গাণিতিক হিসাব করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশি পরিমাপ করতে পারব।
- দূরত্ব ও দ্রুতি নির্ণয় করতে পারব।
- দ্রুতি পরিমাপে স্টপ-ওয়াচ (থামা-ঘড়ি) সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারব।
- অতিরিক্ত গতি কীভাবে জীবনের জন্য ঝুঁকি বয়ে আনে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালে সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদেরকে সচেতন করব।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
প্রিতম স্কুল থেকে পূর্বদিকে সোজাপথে ১৮ মিটার চলল। সেখান থেকে একই পথে একই দিকে ৬ মিটার ফিরে এলো।
মিনা একটি স্থান থেকে নির্দিষ্ট দিকে সোজা পথে ১০ মিটার গেল। 'সেখান থেকে একই পথে পেছনের দিকে ৮ মিটার ফিরে এলো।
সাদিয়া ও নাবিলা ভুল ছুটির পর হেঁটে যথাক্রমে ১০ সেকেন্ডে ১৫ মিটার এবং ২০ সেকেন্ডে ২৫ মিটার গেল।
আমাদের চারপাশে নানা রকম বস্তু রয়েছে। এদের অনেকে স্থির রয়েছে, অর্থাৎ স্থিতিতে রয়েছে, যেমন: ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, গাছ, রাস্তার পাশের ল্যাম্প-পোস্ট ইত্যাদি। এরা এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

আবার অনেক বস্তু আছে যা চলমান বা এদের গতি আছে। যেমন: চলমান ট্রেন, চলন্ত বাস ও গাড়ি, চলমান সাইকেল ও রিকশা, হেঁটে চলা লোক ইত্যাদি।

এবার আসা যাক আমরা স্থিতি ও গতি বলতে কী বুঝি? মনে কর, আনুশেহ রাস্তার এক পাশে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। আনুশেহ বলছে, রাস্তার পাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট ও বাসস্টপ সবই স্থির রয়েছে। সে কেন এ কথা বলছে? বলতে পারবে?
আনুশেহ এ কথা বলছে কারণ এসব বস্তু তার সাপেক্ষে সময়ের সাথে অবস্থান পরিবর্তন করছে না। তাই কোনো বস্তু যদি সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে তা হলে তা স্থির এবং বস্তুর ঐ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি।
| কাজ: হাত দিয়ে একটি কলম ধরে রাখ। তোমার আশেপাশের বস্তুগুলোর সাপেক্ষে কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তুলনা কর। |
তোমার হাতে ধরে থাকা কলমের আশেপাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন: তোমার চেয়ার, টেবিল, তোমার বই, খাতা ও ঘরের সবকিছু থেকে এই কলমের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব ও দিক আছে। কলমের আশেপাশের সকল বস্তুর তুলনায় কলমটির অবস্থান নির্দিষ্ট। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। আমরা বলি, পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি স্থির। কলমটির স্থির থাকার এই ঘটনাই হচ্ছে স্থিতি।
সুতরাং, সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন না করা হলো স্থিতি।
এবার আরেকটি ঘটনা ধরা যাক। আরিয়ান একটি রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। তার সামনে দিয়ে একটা ট্রেন স্টেশন অতিক্রম করে চলে গেল। তা দেখে সে বলল যে, ট্রেনটি গতিশীল। কারণ তার সাপেক্ষে ট্রেনটির অবস্থান প্রতিক্ষণেই পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ আরিয়ানের সাপেক্ষে ট্রেনটি প্রতিক্ষণেই অবস্থান পরিবর্তন করছে।
| কাজ: তোমার হাতে ধরা কলমটিকে এদিক-সেদিক নাড়তে থাকো। আশপাশের সকল বস্তুর সাপেক্ষে কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটছে কিনা তুলনা কর। |
কলমের আশেপাশের প্রত্যেকটি বস্তু থেকে কলমের দূরত্ব ও দিক ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা বলি পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি গতিশীল। সুতরাং, কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি। আমাদের চারপাশে এমন অনেক গতির উদাহরণ হলো, চলমান বাস, কোনো ব্যক্তির দৌড়ে চলা, পাখি উড়ে যাওয়া, ফুটবল গড়িয়ে যাওয়া, গাছ থেকে ফল পড়া ইত্যাদি। তোমরাও এরকম গতির অনেক উদাহরণ দিতে পারবে। বল তো এরকম আর কী কী বস্তুর গতি আছে?
কোনো বস্তু এক পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে স্থির থাকলেও একই সঙ্গে অন্য পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল হতে পারে। একটি ঘটনা বিবেচনা করা যাক, আরিয়ান বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসে বসে থাকা একজন যাত্রী বাসের গতিতে তাকে অতিক্রম করে গেল। আরিয়ানের তুলনায় বা সাপেক্ষে বাস ও বাসের যাত্রী গতিশীল। কিন্তু বাসস্টপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি তার সাপেক্ষে স্থির। কিন্তু বাসের যাত্রীর নিকট মনে হচ্ছে যে গাছটি তার সাপেক্ষে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে।
অর্থাৎ বাসস্টপের গাছটি বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। আরিয়ান যদি ঐ বাসের যাত্রী হতো তাহলে সে দেখতে পেত যে তার সাপেক্ষে ঐ যাত্রীটি স্থির, কিন্তু বাসস্টপের গাছটি তার সাপেক্ষে পিছনের দিকে গতিশীল। একই গাছ আরিয়ানের সাপেক্ষে স্থির কিন্তু বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই পরম স্থিতি বা পরম গতিতে থাকতে পারে না। স্থিতি বা গতি কথা দুটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক এবং নির্ভর করে কে পর্যবেক্ষক তার উপর। কোনো বস্তু কোনো পর্যবেক্ষকের তুলনায় গতিশীল হলেও অন্য পর্যবেক্ষকের তুলনায় স্থির থাকতে পারে। সুতরাং স্থিতি বা গতি পরিমাপের আগে ঠিক করে নিতে হবে কার সাপেক্ষে স্থিতি বা গতি পরিমাপ করা হবে।
| কাজ: একটি সাইকেল নিয়ে তিন বন্ধু মাঠে যাও। এক বন্ধুকে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে বল। তুমি সাইকেলের পেছনের সিটে বস এবং অপর বন্ধুকে সাইকেলটি সোজা চালাতে বলো। তোমরা সাইকেলে চড়া দুই বন্ধু স্থির বন্ধুর সাপেক্ষে প্রতিক্ষণেই অবস্থান পরিবর্তন করছ। |
স্থির বন্ধুর সাপেক্ষে তোমরা কি গতিশীল? হ্যাঁ। কিন্তু তোমার পাশে বসে সাইকেল চালানো বন্ধুটি কি তোমার সাপেক্ষে গতিশীল? অবশ্যই নয়। সুতরাং সকল গতিই আপেক্ষিক।
প্রসঙ্গ-কাঠামো
যে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতি বা স্থিতি পরিমাপ করা হয়, তাকে বলা হয় প্রসঙ্গ-কাঠামো। সুতরাং, প্রসঙ্গ-কাঠামো হলো এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু বা বিন্দু, যার সাপেক্ষে বস্তুর স্থিতি বা গতি নির্ণয় করা হয়। প্রসঙ্গ-কাঠামো হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো বস্তু, যে কোনো স্থান। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এদের সুনির্দিষ্ট হতে হবে। তুমি যদি তোমার বাড়ির সাপেক্ষে একটা রিক্সার গতিবেগ মাপতে চাও, এক্ষেত্রে তোমার বাড়ি হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো। পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের বেগ জানতে চাইলে পৃথিবী হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো।
আমরা জানি, সমগ্র বিশ্বজগৎ গতিশীল। মনে কর, তুমি তোমার বিছানায় শুয়ে আছ। তুমি অবশ্যই বলবে যে, তুমি ভূমির সাপেক্ষে স্থির আছ বা স্থিতিতে আছ। কিন্তু পৃথিবী নিজেই তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। সুতরাং পৃথিবীর সাথে তুমি গতিতে আছ বা গতিশীল।
গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। যেমন:
(ক) চলন গতি
(খ) ঘূর্ণন গতি
(গ) জটিল গতি
(ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি
(ঙ) স্পন্দন গতি বা দোলন গতি
চলন গতি
মনে কর, একটা বাক্স AC-কে কাঠের মেঝের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাক্সের A বিন্দু B বিন্দুতে সরে গেছে এবং C বিন্দু চলে গেছে D বিন্দুর উপর।
এর সকল বিন্দু একই মাপ বরাবর একই দূরত্ব CD পরিমাণ সরে গেছে। এটি হলো চলন গতির উদাহরণ।

সুতরাং, চলন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু এমনভাবে চলে যে এর সকল কণা বা বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।
| কাজ: একটি ইট সংগ্রহ কর। তোমাদের শ্রেণিকক্ষের টেবিলের উপর ইটটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু A তে রাখ। চক দিয়ে দাগ দিয়ে ইটের সামনের ও পিছনের প্রান্ত টেবিলের উপর চিহ্নিত কর। এখন বস্তুটিকে সামনের দিকে ঠেলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যাও। এবার টেবিলে চিহ্নিত ইটের সামনের প্রান্ত থেকে ইটের নতুন অবস্থানের সামনের প্রান্ত এবং শেষ প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মেপে দেখ। |
দেখা যাবে যে, দুটি দূরত্ব সমান। এরকম মধ্যবিন্দু থেকে মধ্যবিন্দু মাপলে দূরত্ব একই পাবে। টেবিলের ড্রয়ারের গতি, ঢালু তল দিয়ে কোনো বাক্স পিছলে পড়ার গতি, লেখার সময় হাতের গতি-এগুলো সবই চলন গতি। চলন গতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) সরল গতি ও (২) বক্র গতি। যখন আমরা লিখি, তখন আমাদের হাত কখনো সোজা বা সরলরেখায় অগ্রসর হয় আবার কখনো বক্ররেখায় অগ্রসর হয়।
যখন কোনো বস্তু সরলরেখা বরাবর চলে, তখন একে সরল রৈখিকগতি বলে। আবার কোনো বস্তু যখন বক্রপথে চলে তখন এর গতি হয় বক্রগতি।

| কাজ: কোনো বন্ধুকে শ্রেণিকক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সোজা হেঁটে যেতে বল। এটা হলো সরল রৈখিক গতি। আরেক বন্ধুকে আঁকাবাঁকা পথে শ্রেণিকক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে বল। এটা হলো বক্রগতি। |
তোমার শ্রেণিকক্ষের সিলিং ফ্যানের গতি লক্ষ কর। চিত্রটি দেখ, এখানে ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেডের ঘূর্ণনের ফলে ক বিন্দু র্ক বিন্দুতে, খ বিন্দু র্খ বিন্দুতে এবং গ বিন্দু র্গ বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়েছে। পাখার প্রতিটি বিন্দু পাখার কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে চলেছে। পাখার এই গতিই হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ। বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে ঘূর্ণনগতি পর্যবেক্ষণ কর।

| কাজ: স্কুলের মাঠে যাও। বাঁশের খুঁটিটি শক্ত করে মাটিতে পোঁত। এক হাত দিয়ে বাঁশটি শক্ত করে ধরে বাঁশের চারদিকে ঘুরতে থাকো। এই গতি হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ। |
তোমরা সাইকেলের চাকার গতি লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই। সাইকেলের চাকা ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হয় বা পথ চলে। এই গতির যেমন ঘূর্ণন আছে তেমন চলন আছে। এই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বা জটিলগতি বলে। গড়িয়ে যাওয়া বলের গতি, ড্রিল মেশিনের গতি হল ঘূর্ণন চলন গতির উদাহরণ।
| কাজ: স্কুলের মাঠে কোনো বন্ধুকে সাইকেল চালাতে বল। সাইকেল চলার সময় এর চাকার গতি লক্ষ্য কর। |
চাকা দুটি কী করছে? ঘুরছে। চাকা কিসের চারদিকে ঘুরছে? চাকা কোনো দূরত্ব অতিক্রম করছে কি? চাকা দুটি এদের কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং প্রতিবারই কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করে। এখানে ঘূর্ণন গতি ও চলন গতি একসাথে কাজ করে। এই গতি ঘূর্ণন চলন গতির উদাহরণ।
ঘড়ির কাঁটার গতি লক্ষ্য কর। সেকেন্ডের কাঁটাটি প্রতি এক মিনিটে একবার এর কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে ঘুরে আসে। কাঁটাটি বারবার একটি পথে একই বেগে ঘুরছে অর্থাৎ এর গতির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ ধরনের গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি।
তোমার স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ের কথা মনে কর। মনে কর, তুমি মাঠের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছ। চারপাক দৌড়ের একজন প্রতিযোগী তোমাকে একই দিক থেকে চারবার অতিক্রম করে যাবে। এটাও পর্যাবৃত্ত গতি। ঘড়ির কাঁটার গতি, পাকদৌড়ের গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি। সুতরাং, কোনো গতিশীল বস্তু যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।

| কাজ: ভালো করে ফোলানো একটা ফুটবলকে প্রথমে উল্লম্ব বরাবর মেঝের দিকে ছুঁড়ে দাও সোজা নিচের দিকে। বলটি যখন মেঝেতে ধাক্কা খেয়ে ওপরের দিকে ফিরে আসবে তখন আবারো তাকে নিচে ঠেলে দাও বারবার এটা করতে থাকো। এ ক্ষেত্রে বলের গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি কারণ এর গতির একটা অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। তুমি যখন বলটাকে বারবার হাত দিয়ে নীচে ঠেলে দিচ্ছো তখন তোমার হাতের গতিও পর্যাবৃত্ত। |
এবার তোমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে এরকম পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ দাও।
কাজ: একটি প্লাস্টিকের রুলার নিয়ে একে টেবিলের এক প্রান্তে এমনভাবে রাখ, যাতে এর বেশ কিছুটা অংশ (প্রায় অর্ধেক) টেবিলের বাইরে থাকে। এবার এক হাত দিয়ে টেবিলের উপরের রুলারের অংশটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধর। যাতে এটি নড়ে চড়ে না যায় এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে। অপর হাত দিয়ে রুলারটির টেবিলের বাইরের অংশটি নিচের দিকে টেনে সামান্য নামিয়ে ছেড়ে দাও।
|
তুমি কী দেখছ? টেবিলের বাইরের রুলারের অংশটি উপরে নিচে উঠানামা করছে (চিত্র ১০.৯) এই ধরনের গতিকে দোলন গতি বা স্পন্দন গতি বলে।
কাজ: সুতার এক প্রান্তে ছোটো নুড়ি পাথরটিকে বেঁধে ছবির মতো করে
|
সুতরাং, দোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সেই পর্যাবৃত্ত গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের দুই পাশে সমান ভাবে চলে বা গতিশীল। দেয়ালঘড়ির দোলকের গতি দোলন গতি।

নে কর, আনিলা কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ১০ মিটার দক্ষিণে গেল। তারপর সে উল্টা দিকে ঘুরে উত্তর দিকে ৪ মিটার গেল। এখানে আনিলা দূরত্ব অতিক্রম করল (১০+৪) মিটার বা ১৪ মিটার। কিন্তু আনিলার সরণ ঘটল মাত্র (১০-৪) মিটার = ৬ মিটার। কেন? কারণ, দূরত্ব হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অতিক্রম করা মোট দৈর্ঘ্য। এখানে তা ১৪ মিটার। আর সরণ হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রম করা সোজাসুজি দূরত্ব। যা হলো (১০-৪) মিটার = ৬ মিটার।
সুতরাং, দূরত্ব হলো যে কোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো নির্দিষ্ট দিকে সোজাসোজি বা সরলরেখার অতিক্রান্ত দূরত্ব। সরণ হলো বস্তুটির প্রথম অবস্থান থেকে বস্তুটির শেষ অবস্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।
উদাহরণ: মিসেস রাশিদা সামনের দিকে ৭ কিলোমিটার হাঁটলেন। এরপর বাঁক নিয়ে পেছনের দিকে ৫ কিলোমিটার হাঁটলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো?
মিসেস রাশিদার অতিক্রান্ত দূরত্ব মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব
= ৭ কিলোমিটার + ৫ কিলোমিটার
= ১২ কিলোমিটার
মিসেস রাশিদার সরণ = সোজাপথে প্রথম থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব = ৭ কিলোমিটার ৫ কিলোমিটার ২ কিলোমিটার
সমাধান কর
রাশেদ সাহেব সকাল বেলা উত্তর দিকে ৪ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে গেলেন। অতঃপর বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে ৭ কিলোমিটার এলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো ?
মনে কর, স্কুল ছুটির পর আনিলা ও নওশীন নভোথিয়েটারে গেল। দুজনেই বিকাল ৫টায় রওনা করল। আনিলা নভোথিয়েটারে পৌঁছাল ৫ টা ৩০ মিনিটে আর নওশীন পৌঁছাল ৫ টা ১০ মিনিটে। কে বেশি দ্রুত গেল? অবশ্যই নওশীন। কারণ নওশীন সমপরিমাণ দূরত্ব আনিলার চেয়ে ২০ মিনিট কম সময়ে অতিক্রম করেছে।
রবিন ও শাহীন তাদের বাড়ি থেকে স্কুলে রওনা করল। রবিন স্কুলে পৌছাল ২০ মিনিটে, শাহীন পৌঁছাল ৪০ মিনিটে। রবিনের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৬০০ মিটার এবং শাহীনের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ২০০০ মিটার। কে বেশি দ্রুত গেল? এখানে রবিন কম দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং শাহীন বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।
কে বেশি দ্রুত গেল তা বের করতে আমাদের বের করতে হবে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে। মনে করা যাক, এই নির্দিষ্ট সময় ব্যবধান হলো ১ মিনিট।
১ মিনিটে রবিনের অতিক্রান্ত দূরত্ব = ১৬০০/২০ = ৮০ মিটার।
১ মিনিটে শাহীনের অতিক্রান্ত দূরত্ব = ২০০০/৪০ = ৫০ মিটার।
সুতরাং, রবিন বেশি দ্রুত স্কুলে গেল। কারণ, সে ১ মিনিটে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সুতরাং কোনো গতিশীল বস্তুর দ্রুতি হলো একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব। এটাকে এভাবেও বলা যায়,
দ্রুতি = দূরত্ব/ দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময়
দূরত্ব মাপা হয় মিটারে, একে সংক্ষেপে 'মি' দিয়ে বুঝানো হয়, সময় মাপা হয় সেকেন্ডে, একে সংক্ষেপে বুঝানো হয় সে. দিয়ে।
উদাহরণ:একটি গাড়ি ৩ সেকেন্ডে ৬০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল। এর দ্রুতি কত?
দ্রুতি = দূরত্ব/ দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময়
= ৬০ মি./৩সে.
= ২০ মি./সে.
সমাধান কর: নাহিয়ান কলেজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ে ৫০০০ মিটার ২৫ মিনিটে গেল। তার দ্রুতি কত?
বেগ
কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।
মনে কর লুবাবা উত্তর দিকে ১০ সেকেন্ডে ১৫ মিটার গেল। তার বেগ কত হবে?
বেগ = ১৫ মিটার/১০ সেকেন্ড
= ১.৫ মি/সে উত্তর দিকে
বেগের মান বলার সাথে দিকও উল্লেখ করতে হবে। কারণ, বেগের মান ও দিক উভয়ই আছে। কিন্তু দ্রুতির শুধু মান আছে। স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাকদৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো দ্রুতির উদাহরণ। এর কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, শুধু মান আছে। নির্দিষ্ট কোনো দিকে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো বেগের উদাহরণ।
মনে রেখ
• কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কোনো বস্তুর সরণ হলো ঐ বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে দূরত্বের সমান।
• সময়ের সাথে কোনো বস্তুর সরণের পরিবর্তনের হারকে বেগ বলে।
মনে কর, একটি মোটর সাইকেল ২০ মিটার/সেকেন্ড বেগে চলছিল। চালক অ্যাকসিলারেটর চাপলেন ফলে মোটরসাইকেলটি আরও বেশি বেগে যেতে লাগল। মনে করা যাক, প্রতি সেকেন্ডে মোটরসাইকেলের বেগ ৫ মিটার/সেকেন্ড বাড়ছে।
মোটরসাইকেলটির আদি বা প্রাথমিক বেগ ছিল ২০ মিটার/সেকেন্ড
১ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ২৫ মিটার/সেকেন্ড
২ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৩০ মিটার/সেকেন্ড
৩ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৩৫ মিটার/সেকেন্ড
৪ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৪০ মিটার/সেকেন্ড
৫ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৪৫ মিটার/সেকেন্ড
প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বেগ বাড়ছে তা হলো ত্বরণ। এখানে প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার/সেকেন্ড বেগ বাড়ছে।
সুতরাং ত্বরণ হলো প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার/সেকেন্ড। একে ৫ মিটার/সেকেন্ড লেখা হয়। মোট সময় এবং ঐ সময়ে বেগের মোট বৃদ্ধি জানা থাকলে সহজেই ত্বরণ বের করা যায়।
এখানে আদি বেগ ছিল ২০ মিটার/সেকেন্ড। শেষ বেগ ছিল ৪৫ মিটার/সেকেন্ড
সুতরাং বেগের মোট বৃদ্ধি (৪৫-২০) মিটার/সেকেন্ড = ২৫ মিটার/সেকেন্ড
মোট সময় লেগেছে ৫ সেকেন্ড
সুতরাং, ত্বরণ = (বেগের মোট বৃদ্ধি)/(মোট সময়)
= (২৫মি/সে)/৫সে = ৫ মি/সে
সুতরাং, ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বেগের বৃদ্ধির হার বা প্রতি একক সময়ে বেগের বৃদ্ধি।
মন্দন
উপরের উদাহরণে মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৫ মি/সে বাড়ছিল। চালক যদি অ্যাকসিলারেটর না চেপে ব্রেক চাপতেন তাহলে মোটরসাইকেলটি ধীরগতি হয়ে যেত। এর বেগ হয়ত প্রতি সেকেন্ডে ৫ মি/সে কমতে থাকত। মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ কমত তাকে বলা হয় ঋণাত্মক ত্বরণ বা মন্দন।
| কাজ: ৫/৬ জন বন্ধু মিলে এক একটি দল তৈরি কর। প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে যানবাহনের দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে আলোচনা কর। আলোচনা শেষে কারণগুলো খাতায় লিখ। প্রতিটি দল থেকে একজন তা উপস্থাপন কর। সকল দলের উপস্থাপনের পর নিজেরা সারসংক্ষেপ তৈরি কর। |
আমাদের দেশে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। এ দুর্ঘটনার একটি কারণ অতিদ্রুত গাড়ি চালানো। অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে যানবাহনের উপর চালকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সুতরাং, যেসব বাসচালক, ট্রাকচালক বা গাড়িচালক অতিদ্রুত গাড়ি চালান, তারাই বেশি দুর্ঘটনায় পড়েন। ফলে অনেক লোক মারা যায়। অনেক লোক আহত হয়। অনেক লোক চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। তাই অতিরিক্ত বেগে বাস, ট্রাক, লরি ও গাড়ি চালাতে নেই। কেউ চালালেও তাকে নিষেধ করতে হবে। সরু রাস্তা, রাস্তার বাঁক ও সেতুতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি। এসব জায়গায় অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক রাস্তায় যানবাহনের গতিসীমা নির্দিষ্ট করা থাকে। এ নির্দিষ্ট গতিসীমা মেনে যানবাহন চালাতে হবে। বড় হয়ে নিজেরা কখনো অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালাবে না এবং অন্যকেও চালাতে নিষেধ করবে।
নতুন শব্দ : স্থিতি, গতি, চলন গতি, ঘূর্ণন গতি, চলন ঘূর্ণন গতি, পর্যাবৃত্ত গতি, স্পন্দন গতি, সরণ, বেগ ও ত্বরণ।
এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম
- কোন বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি।
- কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে, তখন বস্তুটিকে স্থিতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি।
- সকল গতিই আপেক্ষিক।
- গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। যেমন (ক) চলন গতি (খ) ঘূর্ণন গতি (গ) জটিল গতি (ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি (ঙ) স্পন্দন গতি বা দোলন গতি
- কোনো গতিশীল বস্তুর সকল কণা বা বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করলে তাকে চলন গতি বলে।
- কোনো বস্তুর সকল বিন্দু একই পথে না চলে এর প্রতিটি বিন্দু যদি এর কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে চলে তাহলে এর গতিকে ঘূর্ণন গতি বলে।
- যে গতির ঘূর্ণন ও চলন উভয়ই আছে সেই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বলে।
- কোনো গতিশীল বস্তু যদি একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।
- দোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের অগ্রপশ্চাৎ চলে বা গতিশীল।
- দূরত্ব হলো যে কোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো বস্তুর প্রাথমিক অবস্থা হতে শেষ অবস্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।
- কোনো বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে দ্রুতি বলে।
- কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।
- ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হার বা প্রতি সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি।
- মন্দন হলো ঋণাত্মক ত্বরণ।
- যানবাহনের অতিরিক্ত গতি দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ।
Read more